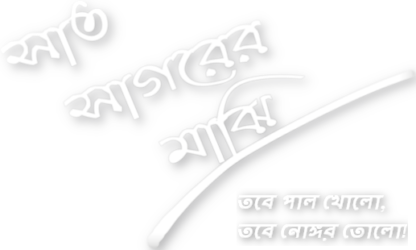যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরপশ্চিমে প্যাসিফিক মহাসাগরের পাশে দুটো সুন্দর স্টেট আছে — ওরেগন আর ওয়াশিংটন। এই এলাকার রেইন ফরেস্টের সুউচ্চ চিরহরিৎ গাছপালা, নয়নাভিরাম তুষারাবৃত পর্বত আর পাথুরে সৈকতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রান্সিস্কো পর্যন্তও বিস্তৃত। ওরেগনে বেশ ক’বছর আগে গ্রীষ্মের কয়েক মাস কাটানোর সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। সেসময়ের অন্যতম স্মৃতি হল এক মার্কিন সহকর্মী বন্ধুর সাথে প্রশস্ত কলাম্বিয়া নদীর তীরে ক্যাম্প করে দু’রাত্রি কাটানো — স্কামানিয়া ফ়োক ফ়েস্টিভাল উপভোগ করার উসিলায়।
সে উৎসবে গেছিলাম মূলত আইরিশ স্টেপ ড্যান্সিং সামনাসামনি দেখার লোভে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকেই এনিয়া–চীফটেইনস প্রমুখ শিল্পীর গান আর স্টারটিভিতে রিভ়ারড্যান্স শো দেখে আইরিশ–কেল্টিক ঐতিহ্যের প্রতি একটা প্রবল আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। হাতে আঁকা ছবির মত নিসর্গের মাঝে খোলা আকাশের নিচে সেই আইরিশ নৃত্য-গীতি-বাদ্য দেখা-শোনা তো হলোই, উপরি হিসাবে পেলাম মার্কিনদেশের নানারকম উপভোগ্য লোকগীতির পরিবেশনা। তার মধ্যে ছিল ফ়োক, ব্লুজ়, জ্যাজ় — আর ব্লুগ্রাস!
এর আগে ব্লুগ্রাস সম্পর্কে আমার ধারণা খুব বেশি ছিল না। শুধুমাত্র যেখানে এর নমুনা পেয়েছিলাম, সেটা হল কোয়েন ব্রাদারস পরিচালিত, জর্জ ক্লুনি অভিনীত অনবদ্য মিউজ়িক্যাল চলচ্চিত্র ‘ও ব্রাদার হয়্যার আর্ট দাউ’। এ লেখার অনুসঙ্গ হিসাবে তার থেকে একটা গান জুড়ে দিলাম।
গানের কথায় বুঝতে পারছেন, গায়ক (বা গীতিকার) দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয় উজাড় করে দিচ্ছে। আমেরিকার দক্ষিণের পাহাড়ী আপালাচিয়া অঞ্চলের কেন্টাকি স্টেটে তার জন্ম। সারাজীবন নানারকম ঝুটঝামেলা তার সঙ্গী। মানে, হয়ত সে সমাজচ্যুত আউটক্যাস্ট, অথবা আইন থেকে পলাতক আউটল’। তার নেই কোন বন্ধু-নিকটজন, যে তার ছন্নছাড়া জীবনে সহায় হতে পারে। পথে হয়ত প্রেমে পড়েছিল, কিন্তু সেখানেও পিছু ছাড়েনি তার অতীত। তাই আবার সে পলায়নপর, হয়ত তার মরণ হবে সে প্রচেষ্টায়। হয়ত প্রেমিকা তাকে ভুলে অন্য কাউকে ভালবাসবে, কিন্তু তাতে তার হাঁহুতাশ নেই! কারণ এ সুনিশ্চিত, যে একসময় না একসময় স্বর্গের স্বর্ণালী সৈকতে আবার দেখা মিলবে দু’জনার!… গানটা যতটা না দুঃখের, তার থেকে বেশি বোধহয় দুর্ভাগ্যপীড়িত অনন্যোপায় গায়কের সান্ত্বনালাভের প্রয়াস। (মুভ়িটা দেখলেই বুঝবেন গানের মাজেজা!)
এখানে গানটা পুরোপুরি ব্লুগ্রাস স্টাইলে গাওয়া হয়নি, কারণ একমাত্র সঙ্গত গীটার। সাধারণত ব্লুগ্রাস গানে গীটারের সাথে ব্যাঞ্জো, ফ়িড্ল, ম্যান্ডোলিন, স্ট্রিং বাস, ইত্যাদি জুড়ি থাকে। কিন্তু মুভ়িতে ক্লুনির কল্পিত ব্যান্ড সগি বটম বয়েজ় নামের সাথে প্রখ্যাত ব্লুগ্রাস ব্যান্ড ফ়গি মাউন্টেইন বয়েজ়ের সুস্পষ্ট মিল। তিরিশ-চল্লিশের দশকে রেডিও আর গ্রামোফ়োন জনপ্রিয় ও সহজলভ্য হওয়া শুরু করে যখন, তখন ১৯১৩তে লেখা এ গানটি আরো অনেকের পাশাপাশি ব্লুগ্রাস শিল্পীরাও রেকর্ড করেন। অধুনাযুগের সবচে’ খ্যাতিমান ব্লুগ্রাসগায়ক রাল্ফ় স্ট্যানলিও এটা গেয়েছিলেন, অ্যালিসন ক্রাউসও। সুতরাং ম্যান অফ় কনস্ট্যান্ট সরো’র ব্লুগ্রাস যোগাযোগ অনস্বীকার্য।
কিভাবে ব্লুগ্রাসের উৎপত্তি হলো, সে কাহিনী ম্যান অফ় কনস্ট্যান্ট সরো’র মতই মর্মস্পর্শী। আমেরিকায় ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত দাসত্বপ্রথা ছিল সে আমরা ভালমতই জানি। যেটা অত ভালমত জানি না, সেটা হলো একই শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষ কিভাবে একরকম দাস হিসাবেই মার্কিনে এসেছিল। এখনকার ভাষায় এদেরকে বলে ইনডেঞ্চারড সার্ভ্যান্ট, বা চুক্তিবদ্ধ চাকর।
ইউরোপীয় জাহাজী আর দালালের দল ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড আর স্কটল্যান্ডের সহায়সম্পত্তিহীন কর্মক্ষম মানুষ পেলে তাদেরকে নতুন বিশ্বের উন্নত জীবন আর সুযোগের কথা দিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে চুক্তিনামায় সই করাত, তারপর আমেরিকায় এনে টাকার বিনিময়ে তুলে দিত তাদের মালিকের কাছে। বিশেষ করে আয়ারল্যান্ডে পরপর কয়েকটি দুর্ভিক্ষের কারণে জীবন বাঁচাতে গরিবদের চুক্তিস্বাক্ষরব্যতীত আর তেমন কোন উপায় ছিল না। চুক্তি অনু্যায়ী যতদিন না সেই চাকর গতর খেঁটেই হোক আর অন্য কোনভাবে হোক, অন্তত তার জাহাজভাড়া না পরিশোধ করছে, ততদিন সে মালিকের আজ্ঞাবাহী। যদি পালায় তো কৃষ্ণাঙ্গ দাসের মতই তাকে খুঁজে বের করে মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার নিয়ম।
তো, এসকল দরিদ্র শ্বেতাঙ্গরা মুক্তির ঋণ পরিশোধ করার পরে যে সাথে সাথে সমৃদ্ধি, জমিজমা পেয়ে যেত, তা নয়! উত্তরের তেরো কলোনির অধিকাংশ ইতিমধ্যে জনবহুল হয়ে গেছে, জায়গাজমির মালিকানা দলিল-দস্তাবেজ হয়ে গেছে। অতএব এরা সুযোগের সন্ধানে যাওয়া শুরু করে দক্ষিণের কৃষিকাজনির্ভর স্টেটগুলিতে। আপালাচিয়ার দক্ষিণাংশের কেন্টাকি, টেনেসি, জর্জিয়া ইত্যাদি স্টেটে কাজ পায় অনেকে। কিন্তু জমির মালিকানা যারা খুঁজছিল, তাদের জন্যে বাকি ছিল অনূর্বর পাহাড়ী জমি। সেসবেই কোনরকমে বসতি গেঁড়ে সাবসিস্টেন্স ফার্মিং আর শিকার করে জীবননির্বাহ শুরু করে তারা।
আর যাদের এতে মন ভরলো না, তারা আর তাদের বংশধরেরা কাউবয়-আউটল’ হিসাবে গিয়ে হাজির হল ওয়াইল্ড ওয়েস্টে। কখনো যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহযোগিতায়, কখনো সরকারের আইনি বিরোধিতা গায়ে না মেখে, নেটিভ আমেরিকানদের হটিয়ে নিজেরাই নিজেদের জায়গা করে নিল। কেউ কেউ ওরেগন ট্রেইলের পাইওনিয়ারদের পথ অনুসরণ করে পশ্চিমের স্টেটগুলিতে হাজির হয়ে গেল।
যারা আপালাচিয়াতে রয়ে গেছিল, অতীতের দারিদ্র্য, স্বল্পশিক্ষা, বর্ণবাদ আর কুসংস্কার এখনো তাদেরকে ছাড়েনি। গৃহযুদ্ধের সময়ে এরা দাসপ্রথার রক্ষক কনফ়েডারেট সরকারকে সমর্থন দিয়েছে, কারণ কৃষ্ণাঙ্গরা মুক্তি পেলে তাদের সীমিত জীবিকায় ভাগীদার বাড়বে। যারা জমির মালিকানাহীন কুলি ছিল তাদেরকে ডাকা হত পো’বয় (পুওর বয়) নামে, ক্রীতদাসদের মত তাদেরও ভোটাধিকার দক্ষিণের স্টেটগুলিতে ছিল না। সে আইনের পরিবর্তন হয় গৃহযুদ্ধে ফ়েডারেল সরকারের জয়লাভের পরে।
হিলবিলি আর রেডনেক নাম দিয়ে অন্যান্য শিক্ষিত সাদারা এদেরকে এখনো কটাক্ষ করে। এদের ভুল বানান, অদ্ভূত উচ্চারণ, কাজ়িন বিয়ে করার রীতি, তাপ্পিমারা পোশাক, আর ঘরে বানানো মদের বোতল সত্তর-আশির দশকেও চলচ্চিত্রে দেখানো হত তাদের স্টেরেওটাইপ বুঝানোর জন্যে। ডেলিভ়ারেন্স মুভিটা দেখতে পারেন উদাহরণ হিসাবে। বলতে পারেন, এধরনের স্টেরেওটাইপিংও একরকম রেসিজ়ম, আর তা না হলেও অনেক নিচু চোখে দেখা। আবার আপালাচিয়ার ধনাঢ্য সাদা চাষী আর ব্যবসায়ীরা যখন রাজনীতিতে ঢুকত, তারা সরল হিলবিলিদের বর্ণবাদ আর অন্যান্য ভয়-বিদ্বেষ উস্কে দিত নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থোদ্ধারের জন্যে। এ কৌশল এখনও খাঁটে।
আইনকানুন মানার ব্যাপারেও হিলবিলিরা একটু অমনোযোগী, আর একরোখা-স্বাধীনচেতা হওয়ায় ম্যান অফ় কনস্ট্যান্ট সরো’র মত ট্রাবলে জড়াতেও সময় লাগে না। দক্ষিণের স্টেটগুলির কড়া আইন অনেকের জীবনে একবার এসে ধরলে বাকি জীবন পিছে লেগেই থাকে।
বুঝতে পারছেন, এ যুগে এরাই সম্ভবত আদর্শ ট্রাম্প সাপোর্টার! অপরদিকে রাল্ফ় স্ট্যানলির মত নামীদামী শিল্পীরা কখনোই রাজনীতিতে ঝোঁক দেখাননি!
ব্লুগ্রাসের সুরের পিছনে এখনো ফ়োক ইংলিশ কিংবা আইরিশ-স্কটিশ একটা ছায়া খুঁজে পাওয়া যায়। ফ়িডলের দ্রুত তালের মধ্যে আয়ারল্যান্ডের জিগস–রীলসের ছন্দের প্রভাব রয়ে গেছে। খুব দ্রুততার সাথে কর্ড পরিবর্তন করার জটিল ইমপ্রোভ়াইজ়েশনও ব্লুগ্রাসের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এমনকি, যতই বর্ণবাদী বলি না কেন হিলবিলিদের, কৃষ্ণাঙ্গদের ব্লুজ়-জ্যাজ় থেকে তারা অনেক কিছু শিখে মিলিয়ে নিয়েছে ব্লুগ্রাসের মধ্যে। বিষয়বস্তুর মধ্যে বিয়োগবেদনার পাশাপাশি রয়েছে অতীতের স্মৃতিচারণ, পূর্বপুরুষদের বীরত্বের জয়গাঁথা, এমনকি প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে বাকবিতন্ডা বা মারামারির উপাখ্যান, কিংবা বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ আর পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে আক্ষেপ-ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। আর সর্বোপরি, গ্রাম্য আপালাচিয়ার সীমিত জীবিকা আর দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপনের কঠিন চিত্র।
ব্লুজ়ের মধ্যে যেমন কৃষ্ণাঙ্গদের জাতিগত বেদনার স্মৃতি রূপান্তরিত হয়ে গেছে সার্বজনীন একটা আবেগপ্রবণতায়, আমি বলবো সেরকম ব্লুগ্রাসও শ্বেতাঙ্গ খেঁটে-খাওয়া মানুষের শ্রেণীগত আশা-নিরাশা-বীরত্ব-ভয়-সুখ-দুঃখ ইত্যাদির ভাবপ্রবণ সরল অভিব্যক্তি।
আশা করি তুলনামূলক স্বল্পপরিচিত একটি মার্কিন শ্বেতাঙ্গ সংস্কৃতিকে কিছুটা হলেও তুলে ধরতে পেরেছি, আর পাঠকরা সামান্য হলেও এদের সহমর্মী হতে পারছেন। ও হ্যাঁ, ও ব্রাদার হয়্যার আর্ট দাউ — দেখতে ভুলবেন না!