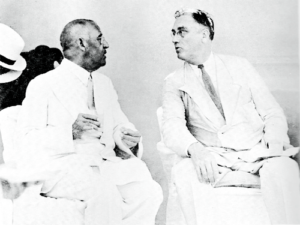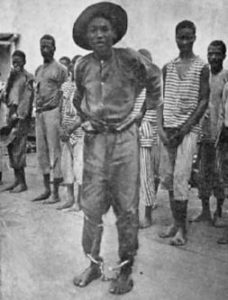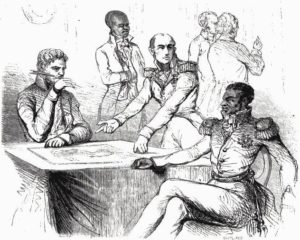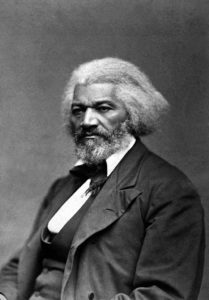জেরুজালেমে উবার ডাকা মানে আসলে ট্যাক্সিই ব্যবহার করা, সেগুলি উবারের পার্টনার। যে চারজন ট্যাক্সি ড্রাইভারের সার্ভিস নিলাম, তাদের মোটে একজন ছিল হিব্রু, বাকিরা আরব।
সিটি অফ ডেভিডে সংরক্ষিত খ্রীষ্টপূর্ব জেরুজালেমের প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ দেখে তাড়াহুড়ো করে বেরুলাম। হোটেল থেকে চেকআউট করতে হবে। কিন্তু পুরো রাস্তা গাড়িভর্তি, উবার ডাকলে কখন এসে পৌঁছবে, খুঁজে পাব কিভাবে নানা চিন্তা। বুদ্ধি করে চলমান ট্যাক্সি দেখে হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে গেলাম। সে ব্যাটা থেমে ইশারা করল ঢোকার জন্য।
পেছনের দরজা খুলতে গিয়ে দেখলাম সেখানে তখনো যাত্রী। কালো-সাদা পোশাক, মাথায় ফেদোরা টুপি, দাঁড়িওয়ালা, লম্বা জুলফি দুই আল্ট্রা-অর্থডক্স ইহুদী বসে আছে, কোলে বড় টুপির বাক্স। গিয়ে বসলাম সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে। পেছনের সীটের যাত্রীদের জানালাম “শালোম”, হাস্যমুখে উত্তর এল “শালোম আলেইখেম” — আমাদের সালাম আলাইকুম।
ড্রাইভার কয়েক ফীট গিয়ে পেছনের যাত্রীদের নামিয়ে দিল। বিদায়ী সম্ভাষণ জানালাম — “শানা তোভা”, শুভ নববর্ষ। এরা নামল মসজিদুল আকসার প্রবেশদ্বার লায়ন্স গেটের বিপরীত দিকে। সম্ভবত ওয়েস্টার্ন ওয়াল বা জুয়িশ কোয়ার্টারে যাবে।
ড্রাইভার যে আরব তার চেহারা দেখেই বুঝেছি শুরুতে। এবার সেই শুরু করল কথোপকথন। কোথা থেকে এসেছি, নাম কি ইত্যাদি। নাম শোনার পর প্রশ্ন, তুমি খ্রীষ্টান না মুসলিম? একটু ভ্রু কুঁচকেছিলাম, কারণ এ প্রশ্ন লেভ্যান্টের হচপচের বাইরে আর কেউ আমাকে করবে না! মুসলিম জানার পর ড্রাইভার স্বপরিচয় দিল, মাহমুদ, আরব মুসলিম। ওয়েস্ট ব্যাংকে চলমান সমস্যা নিয়ে কিছু কথা হল, সমব্যথিতা জানালাম।
কিন্তু সাথে সাথে জিজ্ঞেস করলাম, এই যে পেছনের সীটে “হাসিদী” ভদ্রলোকেরা বসে ছিল, তাদের সাথে তোমাদের সমস্যা নেই? উত্তর এল, এরা? নাহ এরা কোন সমস্যা করে না, রাতদিন আল্লাবিল্লা করে। আমাদের সমস্যা “রেগুলার” ইসরাইলিদের সাথে।
তো সেই “রেগুলার” ইসরাইলি বলতে সে কি বোঝে, তা সুন্দরমত ব্যাখ্যা করে বলতে পারল না। তার পরিবার চার প্রজন্ম ধরে জেরুজালেমের বাসিন্দা, আট সন্তান ঘরে। ট্যাক্সি-উবার চালিয়ে অর্থসংস্থান ভালই হচ্ছে। জেরুজালেমে তেমন কোন ঝামেলা পোহাতে হয় না, কিন্তু তার মন টানে জেনিন-নাবলুসে নিপীড়িত স্বজাতির জন্যে। না, সেসব শহরে তার কোন নিকট স্বজন বা বান্ধব নেই।
যা হোক, এই “হাসিদীরা” আসলে কারা? এদের চেনার সবচেয়ে সোজা উপায় তাদের বেশভূষা। সবসময় সাদা-কালো জামা পরে থাকবে, লম্বা কোট টেল, মাথায় অধিকাংশ সময় ফেদোরা হ্যাট, ইয়া লম্বা বেনি করা জুলফি, মুখভর্তি দাড়ি। পোস্ট করা ভিডিওতে শাবাতের সন্ধ্যায় ওয়েস্টার্ন ওয়ালে গমনরত হাসিদীদের দেখিয়েছি। রোশ হাশানার মত বিশেষ দিনগুলিতে এরা বড় বড় পশমী টুপিও পরে, যাদের নাম শ্ট্রেইমেল। বংশপরম্পরায় এসব টুপি পায় অনেকে, আবার অনেকে বিয়ের সময় “যৌতুক” হিসাবে পায় শ্বশুরের কাছে। মহা দামী টুপি এগুলি। তাই বাঁছা বাঁছা “ঈদের” দিনগুলিতে পরে।
জেরুজালেমে প্রথম দিন ঢোকার সময়ই রাস্তাঘাটে প্রচুর হাসিদী পুরুষ-মহিলা দেখেছিলাম। তেল আবিবের কসমোপলিটান পরিবেশে এদের একদম দেখা যায় না বললেই চলে। যে ইউক্রেনীয় রুশ ড্রাইভার অ্যালেক্স তেল আবিব থেকে নিয়ে এল আমাদের, সে এদের ডাকনাম দিয়েছে “পিনগিন” — পেঙ্গুইন, ভিডিওতে শুনবেন। আমি হাল্কা ডিসক্রিমিনেশনের আঁচ পেলাম। রুশ সমাজে এ ঘৃণা অধুনা পর্যন্ত চলে এসেছে। বের হল, অ্যালেক্স আমাদের আরেক রুশবংশোদ্ভূত ইউক্রেনিয়ান চালক বোয়াজ/বোরিসের মত ইহুদী নয়, রুশ অর্থডক্স খ্রীষ্টান। সে অবশ্য ইংরেজী ভাল পারে না। আমার সিরিলিক জ্ঞান আর গুগলের মাধ্যমে বেশি জটিল কথোপকথন চলল।
হাসিদীদের জন্মস্থলও সপ্তদশ শতকের পোল্যান্ড ও পশ্চিম ইউক্রেন। এখনো ইউক্রেনের উমান শহরে বহু হাসিদী ইহুদী ফিরে যায়, কারণ সেখানে রয়েছে এক বড়সড় গুণী রাবাইয়ের মাজার। আগে এ ব্যাপারে একটা পোস্ট করেছি। আমেরিকার নিউ ইয়র্কেও এদের বড় একটা সংখ্যা বসবাস করে। আমেরিকায় দারিদ্রের হার সবচে বেশি যে শহরে, সেই কিরিয়াস জোয়েল মূলত হাসিদীঅধ্যুষিত।
হাসিদী মেয়েরাও পোশাকআশাকে মডেস্টি চর্চা করে। স্কার্ট পরে ফুল লেংথ, লং স্লীভ জামা। বিবাহিত হলে মাথা ঢাকে। কম দৈর্ঘের স্কার্ট যদি পরে তো পুরু স্টকিং পরবে। ছবি ভিডিওতে এদেরও দেখিয়েছি। এ সমাজে নারীরাই যা অর্থোপার্জন করার করে। পুরুষদের অধিকাংশ সারাদিন তোরা’-তালমুদ পড়ে। সরকারের অর্থপুষ্ট ইয়েশিভা (মাদ্রাসা) থেকে ভর্তুকি পায়। এরা দেশের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠী, বাইরের দানখয়রাতের ওপর নির্ভরশীল। সরকারী ভর্তুকি নিলে ধর্মগ্রন্থ পাঠ ছাড়া অন্য কোন কাজ এরা করতে পারে না। প্রতিরক্ষা বাহিনীতেও এরা এগজেম্পশন পায়, আর ঠেলে পাঠাতে চাইলেও যাবে না। এই নিয়ে ইসরাইলে রাজনৈতিক শোরগোল রয়েছে।
হাসিদীদের তুলনা করা যেতে পারে মুসলিম তবলীগ জামাতের সাথে, কিংবা সুফীদের সাথে। এরা বেশ কম্যুনাল, নিজেদের সমাজের বাইরে মেশে না, অন্য মতের ইহুদীদের সাথেও না। এদের হুজুরদের নাম “রেব্বে”, তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় শ’ থেকে হাজারখানেক পরিবার নিয়ে তৈরি “ডাইনেস্টি।” বছরের বিশেষ দিনগুলিতে এরা একত্রিত হয়ে জিকর মাহফিল ধরনের প্রার্থনা করে, সুফীদের মত ঘুরে ঘুরে নাচে। মহিলাদের নাচা বারণ, বসতে হয় আলাদা। অনেকটা সুফী আধ্যাত্মিকতাবাদ ও গূঢ়তত্ত্বের চর্চা করে এরা।
হাসিদী ছাড়াও সকল ধার্মিক ইহুদী ঘুমানো-গোসল বাদে চব্বিশ ঘন্টা মাথা ঢাকে। সে টুপি হতে পারে কিপ্পার মত ছোট, শুধু চান্দি ঢাকে। হতে পারে মুসলিম কুফী টুপির মত, সেটা অনেক বুখারী ইহুদী পরে। আর পূর্ব ইউরোপ থেকে আসা এই হারেদী-হাসিদীরা কিপার ওপরেও পরবে ফেদোরা-হমবুর্গ ধাঁচের ব্রিমসহ টুপি, আর বিশেষ দিনে শ্ট্রেইমেল। বাক্সের মধ্যে বহন করে এসকল দামি ফ্যামিলি হেয়ারলুম। যেগুলি বহন করছিল আমার ক্ষণিকের সহযাত্রীরা।
শুধু সাদা-কালো রঙের পোশাক পরার মাজেজা হচ্ছে বেশি ফ্যাশন না করে, আর বেশি ক্যাজুয়াল না পরে সাধারন মডেস্ট পরিধান করা। জেরুজালেমে গেলে খেয়াল রাখবেন যে শুধু মুসলিম ধর্মালয় নয়, খ্রীষ্টান-ইহুদী ধর্মস্থলেও শর্টস পরা বারণ। ইহুদীদের মাথা ঢাকা, জুলফি বড় রাখা, দাড়ি না কাটা — এসব ব্যাপারে তাদের ধর্মগ্রন্থেই পরিষ্কার নির্দেশ আছে। তবে ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিতে এমন পরিধান ও আচারের কারণ ভিনদেশে প্রবাসজীবনে ভিন্ন আচারের মানুষ থেকে নিজেদের আলাদা পরিচয় টিকিয়ে রাখা। অন্য জাতির বা ধর্মের চিহ্নধারণ মহাপাপ।
বর্তমান ইসরাইল রাষ্ট্রে আল্ট্রা-অর্থডক্স এ সকল ইহুদীদের সংখ্যা আগের থেকে অনেক বেশি — প্রায় দশ শতাংশ। আর ক্রমবর্ধমান। এদের পরিবারগুলো হয় আরবদের মতই বড়। অনেকে হয়ত জানেন, ইসরাইলে অসংখ্য রাজনৈতিক দল রয়েছে এবং গত পাঁচ বছরে চারটি নির্বাচন হয়েছে সেখানে। সেকুলার, জায়নিস্ট দলগুলির পাশাপাশি রয়েছে ধর্মীয় দল — কনজারভেটিভ ও রিফর্ম ইহুদীদের পাশাপাশি রয়েছে এই হারেদী বা আল্ট্রা-অর্থডক্সদের একাধিক দল।
ওয়েস্টার্ন ওয়ালের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো পরিচালনার অধিকার রয়েছে কেবল হারেদীদের। এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্যান্য দল থেকে ভিন্ন রাজনৈতিক মত পোষন করে। জায়নিস্ট আদর্শতেও এরা বিশ্বাস করে না। ইহুদী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা নয়, এদের মতে সেটা হওয়া উচিত ছিল খোদার দৈব হস্তক্ষেপের মাধ্যমে প্রাকৃতিকভাবে। অর্থাৎ বর্তমান ইসরাইল রাষ্ট্রের ভিত্তিটাকেও এরা প্রকারান্তরে প্রশ্নবিদ্ধ করে রেখেছে।
এ কারণে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে তাদের খাঁপ খায় না। বর্তমান ইসরাইল সরকারের মোর্চায় আরব দলসহ বাম-ডান-কেন্দ্র সকল দল রয়েছে, কিন্তু হারেদীদের কোন প্রতিনিধিত্ব নেই।
সব মিলিয়ে ইহুদীদের মধ্যে আলাদা একটা সেগ্রেগেটেড সমাজ বানিয়ে রয়েছে হারেদী-হাসিদীরা। তাদের প্রায়রিটি ধর্মকর্ম, দেশের রাজনীতিতে কি হল, কার সাথে কার গোলমাল এ নিয়ে খুব একটা মাথাব্যথা বেশির ভাগ আল্ট্রা-অর্থডক্স ইহুদীদের নেই। সারাদিন আল্লাবিল্লা করতে পারলেই এরা মহাখুশি।