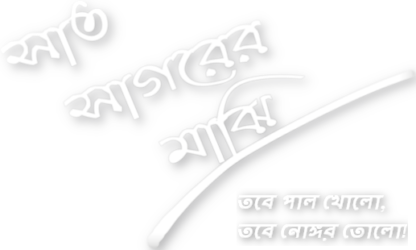আস্তিক হোন কিংবা নাস্তিকই হোন, একথা অস্বীকার করা খুবই কঠিন যে, মানুষের মস্তিষ্কের জৈবরাসায়নিক কম্পোজিশনের মধ্যে মহান অবিনশ্বর কোন শক্তিতে বিশ্বাস আর ‘স্বর্গীয়’ অনুভবের ক্ষমতা মজ্জাগতভাবে প্রোথিত।
অর্গানাইজড রিলিজিয়ন মানুষের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের জন্ম দিলেও ধর্ম অতীতের একেকটা সভ্যতাকে দিয়েছিল একক অবিভক্ত পরিচয়। আর সেসব ধর্মের লক্ষ্য ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়েছে প্রথমত সমসত্ত্ব গোষ্ঠীদের নিজেদের মধ্যে নৈতিকতা আর ন্যায়পরায়ণতার প্রতিষ্ঠায়। তারপর তাদের মূল্যবোধের সম্প্রসারণ হয়েছে অন্য জাত-ধর্মের মানুষকে নৈতিকতার ছত্রতলে এনে, এক ধর্মের বিশ্বাস প্রভাবিত করেছে অন্য ধর্মকেও।
রেনেসাঁস-পরবর্তী যুগের ইউরোপের মনীষীরা অন্যান্য জাতি, ভাষা আর ধর্ম — বিশেষত প্রাচ্যের ইসলাম, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম — সম্পর্কে খুবই কৌতূহলী ছিলেন। তাঁদের জ্ঞান যত বাড়তে থাকলো, তত তাঁদের বোধোদয় হলো যে, একমাত্র খ্রীষ্টধর্মই যে মানুষের আত্মিক সকল চাওয়া-পাওয়ার একমাত্র উত্তর, এধরনের প্রাক-রেনেসাঁস ও রেনেসাঁসযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গি খুবই সংকীর্ণ ও দাম্ভিকতাপূর্ণ।
ফলশ্রুতিতে ভলতেয়ার-মঁতেস্কিউ-পেইনের মত চিন্তাবিদরা যীশুখৃষ্টের আধ্যাত্মিকতাবাদের সাথে প্রাচীন গ্রীস আর মধ্যযুগীয় ইসলামী মনীষীদের যুক্তিবাদী ধ্যানধারণার মিশ্রণের বীজ থেকে উৎপন্ন যে চারায় পানি ঢালা শুরু করলেন, সেটা হলো সার্বজনীন মানবতাধর্মের মতবাদ বা হিউম্যানিজম। আমেরিকার স্থপতিরা টমাস পেইনেরই চিন্তাশিষ্য ছিলেন। মার্কিন সংবিধানের প্রণেতা জেফারসন আর অ্যাডামসের সংগ্রহে বাইবেলের পাশাপাশি তানাখ, কুরান আর গীতা ছিল।
এরকম এনলাইটেনমেন্টের যুগে জন্ম বীটোফেন আর শিলারের। নিচের ভিডিওতে প্রখ্যাত বার্লিন ফিলহার্মোনিক অর্কেস্ট্রা প্রয়াত কন্ডাক্টর হার্বার্ট ফন কারায়ানের পরিচালনায় পরিবেশন করছে বীটোফেনের নবম সিম্ফনির শেষ ‘কোরাল’ অংশটা। সাধারণত শুধুমাত্র বাদ্যযন্ত্র দিয়ে সিম্ফনি কম্পোজ করা হতো। বীটোফেনের নবম হলো সিম্ফনির জগতে কোরাল বা গণসঙ্গীতের প্রথম সফল সূচনা। কোরাল অংশে যে গানটা গাইছে বাস-তেনর-আলতো-সোপ্রানোরা, সেটা শিলারের লেখা কবিতা ‘আন ডি ফ্রয়ডা’ — ‘আনন্দের উদ্দেশ্যে’।
আমার কাছে এই সিম্ফনিটা প্রার্থনাসম! ২৪ মিনিটের হলেও একটু সময় করে শুনে দেখুন! ডাবল বাস্ আর হর্ন সেকশনের গম্ভীর মিউজিক দিয়ে শুরু। এ যেন পুরনো ঘুনেধরা সংকীর্ণ মনোভাবের হতোদ্যম নাভিশ্বাস। অথবা ধরতে পারেন নাপোলেওনের ধ্বংসযজ্ঞে বিধ্বস্ত ইউরোপের নানাজাতের মানুষের ক্লান্তি। তার পরে ক্লারিনেট-ভায়োলিন-ওবো এসে যোগ দিলো সেযুদ্ধে বিজয়ী বীরদের গাঁথা গাইতে, সেও সনাতন সাম্রাজ্যের শৌর্যিক মূল্যবোধেরই নমুনা। এমন সময় বাস সোলোয়িস্ট এসে ভেঙ্গেচুড়ে দিলেন সব: “ও ফ্রয়ন্ডা, নিশ্ট ডিজা ট্যোনা…” — বন্ধু, এ লহরী আর নয়, এসো আজ উৎফুল্লতার গান গাই!
তারপরে শিলারের কাব্য থেকে একে একে উচ্চারিত হলো সকল মানুষের ভ্রাতৃত্ব আর স্বর্গীয়তার ঘোষণা! সেখানে জাতপাত আর ধর্মের বিভাজন নেই, আছে কেবল মনুষ্যত্ব! প্রকৃতিমাতার স্তন্যপানে ভাল-মন্দ সকল জীবের সমাধিকার! বন্ধুত্বের প্রমাণ সেখানে মৃত্যু দিয়ে হলেও তা আনন্দের উচ্চতম শিখর! মানুষ ভাগ্যের কাছে হতদরিদ্র জিম্মি নয়, তার আছে ললাটলিখনকে খন্ডানোর অপরিসীম ইচ্ছাশক্তি! আর আছেন স্রষ্টা! “জাইড উম্শ্লুঙেন, মিলিওনেন! ডিজেন কুস ডের গানৎসেন ভেল্ট!” — কোটি জনতা আলিঙ্গনাবদ্ধ, এই চুম্বন সমগ্র বিশ্বের! “ব্র্যুডের, উ্যবার্ম শ্টের্নেনৎসেল্ট, মুস আইন লিবের ফাটার ভো’নেন!” — ভাইয়েরা, ঐ তারকাখচিত আচ্ছাদনের ঊর্ধ্বে এক স্নেহময় পিতা অবশ্যই আছেন!
১৮২২এ এই সিম্ফনি লেখার আগে ১৮০০ সালের দিকে ত্রিশবছরবয়সী বীটোফেন বধির হতে শুরু করেন, আর সেই বেদনায় তাঁর মনে এসেছিল আত্মহননের চিন্তা। হয়ত তিনি সেই ললাটলিখনকে জয় করেই আরো সাতাশ বছর বেঁচে ছিলেন নবম সিম্ফনিসহ অনেক কালজয়ী স্বর্গীয় সুরলহরীর জন্ম দিতে!